প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে ইঙ্গিত
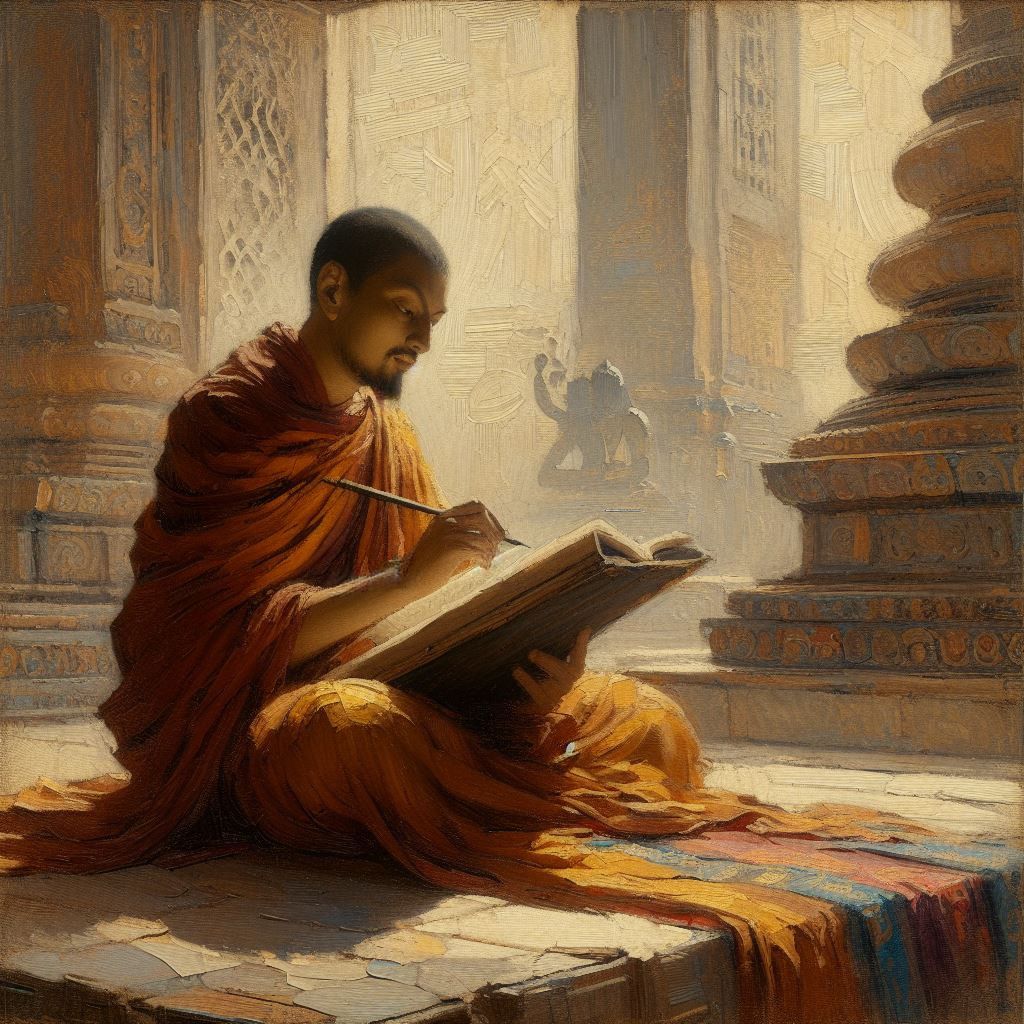
মার্ক্সবাদী সমাজতাত্ত্বিক, মানবতাবাদী দার্শনিক শ্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ‘পৃথিবীর ইতিহাস’ বইটি পড়ছিলাম। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ‘প্রাচীন সমাজ-ট্রাইব থেকে রাষ্ট্র’ অংশটিতে গিয়ে বিশেষ কিছু পড়ছি বলে মনে হলো। এতোদিন বৌদ্ধদর্শনের প্রতি অনেক বাম তাত্ত্বিকের, সমাজবিদের বিশেষ অনুরাগ, আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস, মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত আলোচনায় দর্শনের দিকটি ছাড়াও প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্গত পৌরাণিক কাহিনিগুলোও যে প্রাসঙ্গিক, মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে তা দেখে বিশেষ প্রীত হলাম। তাই এখানে আগ্রহী বন্ধুদের জন্য সেই প্রাসঙ্গিক অংশটি শেয়ার করছি। আশা করি প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে গল্পচ্ছলে বিবৃত আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভ্রূণ এবং তার আগের ক্রমবিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জেনে [বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডারের যে কিঞ্চিৎ অংশ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে] আপনাদের ভালো লাগবে। মূল বইতে সম্পূর্ণ আলোচনাটি পাবেন ১৮৩-১৮৭ পৃষ্ঠায় [এখানে ঈষৎ সংক্ষেপিত]। পড়ে দেখার জন্য আগাম ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে ইঙ্গিত
আমরা আজকাল বলি গণতন্ত্র। কিন্তু ট্রাইব্যাল সমাজে যে রকম চূড়ান্ত গণতন্ত্রের বিকাশ তা সভ্য মানুষের ইতিহাসে আর কখনো সম্ভবই হয়নি। ফলে ট্রাইব্যাল সমাজের এই ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র না বলে সাম্য বলাই ভালো। আমরা আজকাল সাম্যের কথাও বলি। কিন্ত তার সাথে প্রাচীন সমাজের ঐ সাম্যের অনেক পার্থক্য। ফলে ট্রাইব্যাল সমাজকে আদিম সাম্য সমাজ বলা হয়। পশুপালন আর চাষবাস এই দুটি আবিষ্কারের জোরেই মানুষ প্রাচীন সমাজ থেকে সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়েছে।
কিন্তু মানুষের উৎপাদন কৌশল চিরকাল ওই রকম অনুন্নত অবস্থায় থাকেনি। কোথাও বা মানুষ পশুপালন করতে শিখেছে, কোথাও বা শিখেছে চাষবাস। আর এই দুটি আবিষ্কারের ফলেই মানুষের পক্ষে আগেকার তুলনায় অনেক বেশি – অনেক রাশি রাশি জিনিস তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ফলে সম্ভব হয়েছে উদ্বৃত্ত আর উদ্বৃত্তভোগী দলের আবির্ভাব – অর্থাৎ একদল খাটবে আর একদল বসে খাবে, এই তফাত।
কারা শুধু মুখ বুজে খাটবে আর সেই খাটুনির ফল তুলে দেবে অপরের জন্যে? প্রথম অবস্থায় এ ধরনের মানুষ সংগ্রহ হয়েছে যুদ্ধে বন্দীদের থেকেই। তারাই পৃথিবীর প্রথম ক্রীতদাসের দল। ফলে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি সম্ভব হবার পর থেকেই যুদ্ধের উৎসাহও অনেক বেড়েছে। যুদ্ধ করে শুধুই যে অপর ট্রাইবের সম্পদ লুঠ করা সম্ভব তাই নয়, খেটে দেবার জন্যে মানুষ সংগ্রহও সহজসাধ্য।
এদিকে, চাষবাসের উন্নতি হতে হতে মানুষ দেখলো দলের নানান জনের মধ্যে চাষের জমি আলাদাভাবে ভাগ করে নেওয়াই সুবিধের। শুরু হলো জমি ভাগ করে নেবার ব্যবস্থা। কারোর ভাগে পড়লো ভালো জমি। কারোর ভাগে খারাপ জমি। যাদের খারাপ জমি তারা আর নিজেরা নিজেদের জমিটুকু চাষ দিয়ে পেট চালাতে পারে না। ফলে যাদের ভালো জমি তাদের কাছে গতর খাটাতে যায়। এভাবে ট্রাইবেরই কিছু মানুষ ট্রাইবের বাইরে থেকে সংগ্রহ করা ক্রীতদাসদের দলে ভিড়তে লাগলো। ফলে মানুষের দল ক্রমাগতই দুটি স্পষ্ট ভাগে ভাগ হয়ে যেতে লাগলো।
আর যতোই ভাগ হয়ে যেতে লাগলো ততোই দরকার হলো অন্য রকম শাসন ব্যবস্থার। এর সম্পত্তিতে ও হাত দিতে পারবে না। সে বিষয়ে কতকগুলো বাঁধাধরা নিয়মকানুন থাকবে। নিয়মকানুনগুলো সকলেই মানতে বাধ্য। যারা মানলো না তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে – তার জন্যে দরকার সিপাহী সান্ত্রী, জল্লাদ কোটাল, অনেক কিছু। তাদের খরচ চালাবার ব্যবস্থা থাকা চাই – সকলকেই খাজনা দিতে হবে, সেই খাজনা থেকে তাদের খরচ চলবে। শাসন চালাবার জন্যে এই যে এতো রকম নতুন ব্যবস্থা তার পুরোটিকে বলা হয় রাষ্ট্রব্যবস্থা। প্রাচীনকালের সমানে সমান সম্পর্কের ধ্বংসস্তূপের উপরই রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়েছে।
কোন দেশে ঠিক কীভাবে ট্রাইব ভেঙে রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়েছে সে কথা এখনো আমরা স্পষ্টভাবে জানি না। ইতিহাসবিদরা এ নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেননি। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলো বিচার করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার মধ্যে ট্রাইব্যাল সমাজের অনেক রকম স্মৃতিচিহ্ন টিকে রয়েছে। যারা এইসব সভ্যতা গড়ে তুলেছিলো তারা ট্রাইব্যাল সমাজেই বাস করতো।
ট্রাইব ভেঙে কীভাবে রাষ্ট্রের উদয় হয়েছে তার কিছুটা আভাস হয়তো পাওয়া যেতে পারে পুরনো কালের পৌরাণিক কাহিনি থেকে। এখানে একটা নমুনা উদ্ধৃত করবো। বৌদ্ধদের একটি প্রাচীন পুঁথি আছে। তার নাম মহাবস্তু অবদান। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেই পুঁথি থেকে রাজার আবির্ভাব কাহিনি সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা করেছেন [যা নিম্নরূপ]।
“যখন সৃষ্টি হয়, লোকের থাকিবার স্থান হয়, কতকগুলো ‘স্বত্ত্ব’ আভাম্বর হইতে নামিয়া পৃথিবীতে উৎপন্ন হন।…তাহাদের আহার প্রীতি এবং বাড়িঘর সুখ। সুখনিবাসে থাকিয়া তাহারা প্রীতি ভক্ষণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। তাহারা যাহা করেন সবই ধর্ম।
‘তাহার পর পৃথিবী উদয় হলো – যেনো একটি হ্রদ, পানিতে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর রস খাইতে খাইতে তাহাদের রঙও সেইমত হইয়া গেলো। এইরূপে অনেকদিন যায়। যাহারা অধিক আহার করেন তাহাদের রঙ খারাপ হইয়া ওঠে, আর যাহারা অল্প আহার করেন তাহাদের রঙ ভাল থাকে। ভাল রঙের লোকে মন্দ রঙের লোককে অবজ্ঞা করে। সুতরাং আমি বড় তুমি ছোট এই মান-অভিমান জাগিয়া উঠিলো। একদিন যে ধর্ম তাহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিলো, অভিমানের উদয়ে তাহাদের সে ধর্মের প্রভাব খর্ব হইয়া গেলো। পৃথিবী হইতে সে রসও লোপ পাইয়া গেলো। তখন তাহারা খান কি? পৃথিবীর সর্বত্র ভুঁইপটপটি উঠিলো…ক্রমে তাহারা ভুঁইপটপটি খাইতে লাগিলেন। ভুঁইপটপটির মত তাহাদের রঙ হইলো। এইরূপে কত কাল-কালান্তর কাটিয়া গেলো। ভুঁইপটপটির লোপ হইলো, তাহার জায়গায় বনলতা জন্মাইলো। লোকে তাহাই আহার করিতে লাগিলেন।
‘তাহাদের রঙ বনলতার মতই হইয়া গেলো। ক্রমে বনলতার বেলায়ও মান-অভিমান আসিয়া জুটিলো, বনলতারও লোপ হইলো। এবার আসিলেন শালিধান। এ ধানের কণা নাই, তুষ নাই, অতি সুগন্ধ। এই ধান খাইয়া লোকে কতকাল রহিলো। প্রথম প্রথম সকলেই সকাল-সন্ধ্যা দুইবেলা ধান ঝাড়িয়া আনিতো, সঞ্চয়ের নামটিও করিতো না। কিন্তু ক্রমে দু’একজন ভাবিলো, দু’বেলাই ধান কাটিতে হইবে কেন? এক বেলাতেই দু’বেলার ধান যোগাড় করিয়া আনি। তাহারা তাহাই করিতে লাগিলো। তাহাদের দেখাদেখি অনেকেই সেইরূপ করিতে লাগিলো। বরঞ্চ সঞ্চয়ের মাত্রা বাড়িয়া গেলো। এখন আর দু’বেলার সঞ্চয়ে কুলায় না, দুই দিনের সঞ্চয় হইতে লাগিলো, ক্রমে সপ্তাহেরও সঞ্চয় হইতে লাগিলো।
‘ওদিকে কণাওয়ালা, তুষওয়ালা ধান ক্ষেত না করিলে আর জন্মায় না। কতকগুলো দুষ্ট লোকে অন্যায় করিয়া সঞ্চয় করিতে গিয়া আমাদের এমন সুখের খোরাকে ছাই দিলো। যাহা হউক, এখন আমাদের এক কাজ করিতে হইবে। এখন ক্ষেত ভাগ করিতে হইবে, সীমাসরহদ্দ বাঁধিয়া দিতে হইবে…এই ক্ষেত তোমার, এই ক্ষেত আমার, এই ক্ষেত রামের, এই ক্ষেত শ্যামের এইরূপ আবার কিছুদিন চলিলো।
‘একজন বসিয়া ভাবিতে লাগিলঃ আমার তো এই ক্ষেত, এই ধান। যদি কম জন্মায় কী করিয়া চলিবে? সে মনে মনে ঠাহরাইল, দিক আর না দিক, অন্যের ধান আমি তুলিয়া লইব। সে আপনার ধানগুলো সঞ্চয় করিয়া অপরের ক্ষেত্রের ধানগুলো উঠাইয়া আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া কহিলো, ‘তুমি কর কি? পরের ধান তাহাকে না বলিয়া তুলিয়া আনিতেছো?’ ‘আর এরূপ করিব না।’ কিন্তু আবার সে পরের ধান না বলিয়া তুলিয়া আনিলো। তৃতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া বলিলো, ‘তুমি ফের এই কাজ করিলে?’ সে বলিলো, ‘আর এরূপ হইবে না।’ কিন্তু কিছুদিন পরে সে আবার পরের ধান উঠাইয়া আনিলো। তৃতীয় ব্যক্তি এবার আর চুপ করিয়া রহিলো না। সে তাহাকে বেশ উত্তম-মধ্যম দিয়া দিলো। তখন ধানচোর চিৎকার করিতে লাগিলো, -‘দেখ ভাই আমাকে মারিতেছে, দেখ ভাই আমাকে মারিতেছে। কী অন্যায়, কী অন্যায়!’ এভাবে পৃথিবীতে চুরি, মিথ্যা কথা ও শাস্তির প্রাদুর্ভাব হইলো।
‘তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলো – আইসো, আমরা একজন বলবান, বুদ্ধিমান, সকলের মান যোগাইয়া চলে, এমন লোককে আমাদের ক্ষেত রাখিবার জন্য নিযুক্ত করি। তাহাকে সকলে ফসলের অংশ দিবো। সে অপরাধের দণ্ড দিবে, ভাল লোককে রক্ষা করিবে, আর আমাদের ভাগমত ফসল দেওয়াইয়া দিবে। তাহারা একজন লোক বাছিয়া লইল। সকলের সম্মতিক্রমে সে রাজা হইল, এজন্য তাহার নাম হইল মহাসম্মত। এইরূপে তেজোময় জীব অনন্ত আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমে লোভে পড়িয়া মাটিতে মাটি হইয়া গেল। শেষে তাহাদের ক্ষেত আগলাইবার জন্য একজন ক্ষেতওয়ালার দরকার হইল। সেই ক্ষেতওয়ালাই রাজা, ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ তাহার মাহিনা।”
[নোটঃ বন্ধুগণ, মহামতি কার্ল মার্ক্সের সমাজ বিশ্লেষণ এর চেয়ে খুব আলাদা কিছু কি?]
লেখক: ধীমান ওয়াংজা
[লেখাটি তার ফেসবুক ওয়াল থেকে সংগৃহীত]


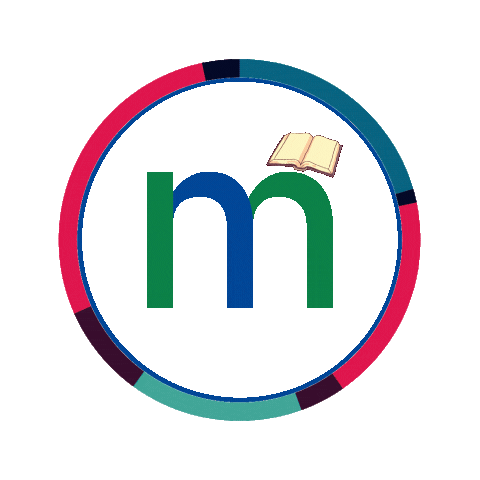


 জীবনী ও স্মৃতিকথা
জীবনী ও স্মৃতিকথা আত্ম-উন্নয়ন
আত্ম-উন্নয়ন ইতিহাস
ইতিহাস এথনো পলিটিক্ম
এথনো পলিটিক্ম অর্থনীতি
অর্থনীতি চিঠিপত্র
চিঠিপত্র আদিবাসী
আদিবাসী আন্তর্জাতিক বিষয়
আন্তর্জাতিক বিষয় গবেষণা
গবেষণা